ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাত যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখান থেকে অর্থনীতিকে ঠিক পথে টেনে তোলা ও বেগবান করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জের কাজ। শুধু অর্থনীতি নয়, প্রায় সব খাতেই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সংকট অন্তর্বর্তী সরকারকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নটি নিবিড়ভাবে যুক্ত। এ বিবেচনায় অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য ছয় মাস যথেষ্ট সময় নয়। কিন্তু রপ্তানি, প্রবাসী আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছাড়া অর্থনীতির বেশির ভাগ খাতের সূচক খারাপের দিকে যাওয়া স্বস্তিদায়ক নয়। অর্থনীতির প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের মনোযোগ যে কম, এটি তারই প্রতিফলন।
বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের ‘বাংলাদেশের অর্থনীতি: ২০২৪-২৫ সংকটময় সময়ে প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, রাজস্ব আদায়, মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান, বেসরকারি বিনিয়োগ, মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি, পুঁজিবাজার ও বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি কোনোটাই ভালো নয়। এটা সত্যি যে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনতে গেলে যেসব কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সমাধান করা প্রয়োজন, সেখানে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ লাগবে। কিন্তু ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নতির জন্য জরুরি ভিত্তিতে যেসব উদ্যোগ সরকার নিতে পারে, সেসব জায়গায় দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলা যায়। ব্যবসায়ী, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে বারবার বলার পরও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান কোনো উন্নতি হয়নি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে কিংবা জ্বালানি তেলের দাম কমাতে, কিংবা শিল্পে গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করতেও সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি।
রাজস্ব বাড়ানো ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের যেখানে পুরোনো ধারা থেকে বেরিয়ে এসে সৃজনশীল পথ অবলম্বন করা জরুরি ছিলো, সেখানে কিছু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উল্টো গত সরকারের ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে। এটা অভ্যুত্থানের যে জন-আকাক্সক্ষা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
সিপিডির তথ্য জানাচ্ছে, চলতি অর্থবছরের অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৭ ভাগ। সরকারের সামনে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বাড়ানোর বড় সুযোগ ছিলো। কিন্তু তারা পণ্য ও সেবায় ভ্যাটের মতো পরোক্ষ কর বাড়িয়ে রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এ সিদ্ধান্ত এসেছে যখন মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপর। একদিকে মূল্যস্ফীতি কমানোর প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে পরোক্ষ কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে স্ববিরোধিতার চিত্রকেই সামনে আনে। গ্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে চুরি ও সিস্টেম লস বন্ধ না করে এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে দেনা আদায় না করে, শিল্প খাতে গ্যাসের দাম বাড়ানোর চিন্তা চলছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত ভীষণ চাপে থাকা অর্থনীতির জন্য হবে আত্মঘাতী।
অর্থনীতির নীরব ঘাতক মূল্যস্ফীতি না কমলে জনমনে স্বস্তি ফিরবে না। অথচ বাংলাদেশের বাজারে পণ্যের দাম বিশ্ববাজার থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি। এর কারণ পণ্য আমদানিতে একচেটিয়াবাদ এবং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের নেটওয়ার্ক। পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছুতে কয়েক দফা হাত বদল হয়। সিপিডি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছে, বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেল কিংবা চিনির দাম বাংলাদেশের বাজার থেকে অনেকটাই কম। চালের বাজার নিয়ন্ত্রণেও সরকারের কার্যকর ভূমিকা নেই। কৃষক কেজিপ্রতি চালের দাম পান ৩৩ টাকা, আর সেই চাল ভোক্তাকে কিনতে হয় ৬৮ টাকায়।
বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারার কি যুক্তি আছে সরকারের? অর্থনীতির কঠিন চ্যালেঞ্জের সময়ে যে ধরনের গতিশীল নেতৃত্ব ও দলগত প্রয়াস দরকার, তার বড়সড় ঘাটতি যে রয়েছে, সিপিডির পর্যালেচনা সেটিকেই আবার সামনে আনল। অন্তর্বর্তী সরকারের এই বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।
পূর্ববর্তী পোস্ট
চুয়াডাঙ্গার তেঘরীর ইব্রাহীমকে মারধর করে টাকা ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ
পরবর্তী পোস্ট
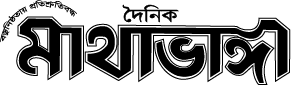

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়, কিন্তু ট্র্যাকব্যাক এবং পিংব্যাক খোলা.